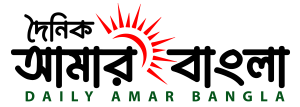- প্রফেসর ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান
প্রথমে ছাত্র এবং পরে শিক্ষক হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে আমার সম্পর্ক পাঁচ দশকেরও বেশি সময়ের। ১৯৭০ সালে ছাত্র হিসেবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম। ১৯৭৮ সালের জানুয়ারিতে একই বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করি। আমার বাবা সাবেক আইন সচিব ও বিচারপতি মো: আব্দুল কুদ্দুস চৌধুরী বরাবরই আমাকে শিক্ষক হতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেছিলেন চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে। ইতঃপূর্বে এ সম্পর্কে আমি এই কলামে লিখেছি। ২০২০ সালের জুনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরোপুরি অবসর গ্রহণ করি। মাঝে সরকারের ওষুধ প্রশাসন অধিদফতরের পরিচালক, বিসিএসআইআর’র চেয়ারম্যান এবং (লিয়েনে) মানারাত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসেবে সব মিলিয়ে সাড়ে ১০ বছরের মতো দায়িত্ব পালন করি। এসব দায়িত্ব পরোক্ষভাবে আমার শিক্ষকতা ও গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। তখনো আমি বছরে গড়ে পাঁচ-ছয়টি গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশ করেছি। শিক্ষকতাকে আমি আনন্দের সাথে নিই এবং গবেষণা ছিল আমার জন্য আরো বেশি আনন্দের। নিজেকে গবেষক হিসেবে পরিচয় দিতে আমার বেশি ভালো লাগে।
গবেষণা করার সুযোগ আছে বলে শিক্ষকতাকে বেশি উপভোগ করেছি। শিক্ষক হিসেবে শিক্ষার্থীদের সাথে আমার হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক সবসময় ছিল। আমি তাদের ভালোবেসেছি এবং তারাও আমাকে গভীরভাবে ভালোবেসেছে। যদিও এই মূল্যায়নটি পূর্ণাঙ্গভাবে শিক্ষার্থীরাই করবে। কিন্তু সবসময় নিজেকে একজন ভালো শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। শিক্ষকতা জীবনের একেবারে শুরু থেকে আমার কাছে শিক্ষার্থীদের অবাধ প্রবেশের সুযোগ ছিল। আসলে শিক্ষার্থীদের সাথে সুসম্পর্ক রেখেই তাদের পড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমি যেসব বিষয় পড়াতাম সেগুলো ছিল কিছুটা কঠিন। তাই চেষ্টা করতাম যেন ছেলেমেয়েরা একঘেয়েমি বোধ না করে। মাঝে মধ্যে হাস্যরস, কৌতুক ইত্যাদির অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পাঠে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতাম। শিক্ষার্থীদের সঙ্গ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তাদের সাথে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শিক্ষা সফরে গিয়েছি। দেশের বাইরেও গিয়েছি। তখনো তাদের ভালোবাসায় আপ্লুত হয়েছি। আমি শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক সবসময় উপভোগ করেছি।
আমি যে বিষয়ে পিএইচডি করেছি তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোই পড়ানোর সুযোগ পেয়েছি। এটা আমার জন্য বাড়তি সুযোগ ছিল। গবেষণালব্ধ বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাত্ত্বিক ক্লাসে শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরতে পেরেছি। মোট কথা আমি যে জ্ঞান অর্জন করেছি সেটি প্রয়োগও করতে পেরেছি। সবাই এই সুযোগ পান না। আমাদের অনেকে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে গবেষণা করেন, পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরেন; কিন্তু তাদের সেই গবেষণা কাজে লাগাতে পারার মতো সুযোগ, উন্নতমানের ল্যাব ও আনুষঙ্গিক পরিবেশ এখানে নেই। এ কথা আমি আগেও বলেছি। আমি ঔষধি গাছ নিয়ে গবেষণা করেছি। এটা বাংলাদেশের জন্য উপযোগী ছিল। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশীয় কবিরাজ, হেকিমরা রোগ নিরাময়ে বনজ বৃক্ষ, গুল্ম, লতাপাতা থেকে তৈরি ওষুধ ব্যবহার করে আসছেন। আমার গবেষণা ও পড়ানোর বিষয় একই হওয়ায় শিক্ষকতা করতে গিয়ে কখনো বিরক্ত বোধ হয়নি। শিক্ষক হিসেবে আমি পরিতৃপ্ত। শতাধিক শিক্ষার্থীর গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। অনেক শিক্ষার্থী আমাদের সুপারিশে আমেরিকা, জাপান, ইউরোপে পিএইচডি করতে গেছে। যখন শুনতাম আমার সুপারিশে কোনো ছাত্র পিএইচডি করার সুযোগ পেয়েছে, স্কলারশিপ পেয়েছে তখন যে আনন্দের অনুভ‚তি হতো তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সবসময় চাওয়া ছিল আমার ছাত্ররা ভালো করেছে, করছে, করবে।
ফার্মেসি বিভাগের ছাত্ররা দেশের ওষুধ শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি প্রশাসনে উচ্চপদে কাজ করছে। ওষুধ শিল্প মালিকদের মধ্যেও আমার ছাত্ররা রয়েছে। আমার বিদেশে চলে যাওয়ার অনেক সুযোগ ছিল। তা করিনি বলে আজ আমার তৈরি করা ছাত্রছাত্রীরাই দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এভাবে আমিও দেশের সেবায় কিছুটা অবদান রাখতে পেরেছি ভাবলে ভালো লাগায় মনটা ভরে যায়। দেশের ওষুধ শিল্পের প্রসারে কিছুটা অবদান রাখতে পেরেছি ভাবলে মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। আমি কিছু দিনের জন্য এখন আমেরিকায়। এখানেও আমার অনেক ছাত্র আছে। তাদের অনেকের সাথে দেখা হয়েছে। আমার ছাত্র এখানকার ‘ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে’ চাকরি করছে। অন্যান্য বিভাগেও কাজ করছে। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্পে আজকের যে পরিবর্তন তাতে ফার্মেসি বিভাগের শিক্ষার্থীদের অনেক অবদান রয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমি শুধু ছাত্র পড়াইনি; শিক্ষকদের কল্যাণে শিক্ষক সমিতির কার্যক্রমে অংশ নিয়েছি, নির্বাচন করেছি। কখনো জিতেছি, কখনো হেরেছি। তখন এর সাথে কোনো রাজনৈতিক দলের ভাবধারার সংযোগ ছিল না। পুরোপুরি রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে আমরা সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করতাম। এটা আমাকে অনেক শিক্ষকের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়।
উপরোক্ত কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো দেশের সর্বপ্রাচীন ও প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তিতে আমিও এর অংশীদার হতে পারার গৌরবের অংশীদার হওয়া। যদিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য এ স্বল্প পরিসরে বলে শেষ করা যাবে না। ১৯২১ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হলেও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এটাকে প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হয় আরো এক দশক আগে, ১৯১১ সালে। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর যখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দেয়া হয় তখন এই উপমহাদেশের যারা মুসলমানদের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ভালো চোখে দেখতেন না, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছেন। তাদের মধ্যে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিও ছিলেন। তারা মনে করতেন এ অঞ্চলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় হলে কলকাতাকেন্দ্রিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর প্রভাব খর্ব হবে। আবার আব্বাও কলকাতাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পড়াশোনা করেছেন। পূর্ববঙ্গ থেকে ছাত্রদের উচ্চতর পড়াশোনার জন্য তখন কলকাতায় যেতে হতো। সেখানে গিয়ে থাকতে হতো। ফলে এখানকার অনেক মেধাবী ছাত্রের সেখানে গিয়ে থেকে পড়াশোনা করার মতো আর্থিক সামর্থ্য ছিল না।
এ অঞ্চলের বেশির ভাগ মানুষ ছিল কৃষক। তাদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। আর জমিদারদের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু। তাদের কাজ-কারবার ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। ফলে ভাটি বাংলা ছিল অবহেলিত। তাই এখানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমরা পড়াশোনার সুযোগ পাবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এটি প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব রাখা হয়। কিন্তু শুরু থেকেই এ প্রস্তাব অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তারা মনে করতেন এই অঞ্চলের মুসলমানরা এখনো শিক্ষাদীক্ষায় উন্নতি করার মতো অবস্থায় পৌঁছেনি। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ঢাকার নবাবরা বিশেষ করে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ বিপুল পরিমাণে ভূসম্পত্তি দান করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা পাকিস্তান আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন থেকে শুরু করে মহান স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।
আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ১৯৪৭ সালে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির ধারাবাহিকতাতেই সেই ভূখণ্ডের ওপর আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সেদিন পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তারা এই অঞ্চলের অবহেলিত মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন করতে চেয়েছিলেন। তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে যাদের অপরিসীম অবদান রয়েছে; তাদের ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়াও আমাদের কর্তব্য।
শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-ঐতিহ্য-অবদান-শিক্ষা-গবেষণা নিয়ে অনেক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম হচ্ছে। তবে এটা ঠিক, শুরু থেকে এমনকি পাকিস্তান আমলেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা ও গবেষণার যে মান ছিল সেটি আমরা ধরে রাখতে পারিনি। একসময় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে ‘অক্সফোর্ড অব দ্য ইস্ট’ বলা হতো। এখন বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের র্যাংকিংয়ে এর অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। কেন এমনটা হয়েছে এ ব্যাপারে অনেকে অনেক কথা বলছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল মুক্তবুদ্ধি চর্চার কেন্দ্র হিসেবে। এর শিক্ষকদের চিন্তা করার স্বাধীনতা থাকবে, বাকস্বাধীনতা থাকবে। তারা সরকারের যেকোনো নীতির সমালোচনা করতে পারবেন। এর ভিত্তিতেই ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল।
পাকিস্তান আমলে শিক্ষকরা লেকচারার হিসেবে জয়েন করার পর সিনিয়র লেকচারার, রিডার তারপর প্রফেসর পদে উন্নীত হতেন। বাংলাদেশ হওয়ার পর শিক্ষকদের পদক্রম অনেকটা আমেরিকান আদলে সাজানো হয়। পাকিস্তান আমলে এখনকার মতো পালাক্রমে বিভাগীয় প্রধান হওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। আগে প্রফেসর বা রিডার ছাড়া কেউ বিভাগীয় প্রধান হতেন না। তখন প্রফেসর সংখ্যাও কম ছিল। যাদের বিভাগীয় প্রধান করা হতো তারা দীর্ঘ দিন একই পদে থাকতেন। যারা বিভাগীয় প্রধান হতেন তারাও খুবই খ্যাতনামা লোক ছিলেন। তাদের অনেকে দেশে-বিদেশে পরিচিত ছিলেন। তবে তখন শিক্ষকদের স্বাধীনতা অনেকাংশে খর্ব ছিল। যদিও একাডেমিক অঙ্গনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ থাকবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু এক ব্যক্তি থাকলে তার মেজাজ মর্জির ওপর শিক্ষকদের পদোন্নতিসহ অনেক কিছু নির্ভর করে।
স্বাধীনতার পর শিক্ষকরা বঙ্গবন্ধুর কাছে গেলেন। এরপর ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এতে আগের নিয়মকানুন অনেকটাই পরিবর্তন করা হয়। তখন আমার বাবা আইন মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সেকশন অফিসার ছিলেন। প্রফেসর এমাজউদ্দীন স্যার এক অনুষ্ঠানে আমাকে বলেছিলেন, সে সময় বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের বলেন যে, আপনারা কুদ্দুস সাহেবের কাছে যান। ওনারা তার কাছে যান এবং ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের খসড়াটি আমার বাবা তৈরি করে দেন। এই অধ্যাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেক বেশি ‘ফ্রিডম’ দেয়া হয়েছে। তাতে কোনো শিক্ষকের রাজনীতি করা বা রাজনৈতিক দলের পদ গ্রহণের পথে কোনো বাধা রাখা হয়নি। যদিও এ ধরনের অতি স্বাধীনতা দেয়ার বিষয়টি আমার পছন্দসই ছিল না। এখানে আরো ‘চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সের’ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হতো।
শিক্ষক সমিতি, সিনেট ইত্যাদিতে যখন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি ঠিক করার প্রশ্ন এলো তখন দলীয়করণের বিষয়টিও সেখানে যুক্ত হয়ে গেল। এখন তো সভা-সেমিনারে অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির আলোচনায় শুনতে পাই যে, শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও গবেষণার মান অনেক নিচে নামিয়ে দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান সৃষ্টির জায়গা। জ্ঞান সৃষ্টি হয় গবেষণার মাধ্যমে। এরপর সেই জ্ঞান বিতরণ হয়। কিন্তু নির্বাচনকেন্দ্রিক রাজনীতিতে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত হওয়ায় শিক্ষার আগের গুণগত মান নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ সিন্ডিকেটের সতেরোটি পদের মধ্যে আটটি শিক্ষকদের মধ্য থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়। তাই সেখানে শিক্ষকরা যে মতামত দেন সেটিই সেখানে প্রাধান্য পায়। সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়োগসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে শিক্ষকরা পরোক্ষভাবে একই সাথে নিয়োগকৃত ও নিয়োগকর্তা হয়ে দাঁড়ান। যদিও নির্বাচনের মাধ্যমে সিন্ডিকেটে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচনে তেমন আপত্তির কিছু নেই। অন্যান্য দেশেও এটা আছে। কিন্তু যারা নির্বাচনে দাঁড়ান তারা নিজেদের পক্ষে জনমত বাড়াতে চান। যখন নির্বাচিত হয়ে সিনেটে যান তখন তার সমমনা বিশেষ করে রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দানের প্রবণতা তৈরি হয়। বিশ্ববিদ্যালয় বা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা থাকেন তারাও চান যে তাদের পক্ষের লোক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। তখন মেধার সাথে আপস করা হয় এবং দলীয় পরিচয়টি বড় হয়ে ওঠে।
যত দিন এ ধারার নির্বাচন থাকবে তত দিন অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। যেমন ডিন নির্বাচন। আমি মনে করি সিনিয়র-মোস্ট কোনো প্রফেসরকে এমনিতেই ডিন করা যায়। দায়িত্বটি বিভাগীয় প্রধানের মতো তিন বছর পরপর পরিবর্তনশীল হতে পারে। বিভাগীয় প্রধানের ক্ষেত্রে সমস্যা না হলে, ডিনের ক্ষেত্রেও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া সিন্ডিকেটে নির্বাচিত শিক্ষকদের মধ্যে প্রভোস্ট থাকারও কোনো কারণ দেখি না। প্রভোস্ট পুরোপুরি একটি প্রশাসনিক পদ। সিন্ডিকেটের পদগুলো আর নির্বাচন প্রক্রিয়ারও সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মনে করি। এখন সিন্ডিকেটে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপক, ডিন ও প্রভোস্টরা একজন করে প্রতিনিধি নির্বাচন করে সিন্ডিকেটে সদস্য হিসেবে পাঠান। ভিসি ও প্রোভিসি পদাধিকার বলে এর সদস্য থাকেন। এর পরিবর্তে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপকরা সাউন্ড একাডেমিক পটভূমির সিনিয়র অধ্যাপকদের যদি সিন্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত করেন; সেই সাথে সরকার জনপ্রিয়তা না দেখে সিনিয়র ও একাডেমিক ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ ব্যক্তিত্বকে ভিসি ও প্রোভিসি পদে নিয়োগ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক একাডেমিক পরিবেশ উন্নয়নে তা সহায়ক হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। প্রতিটি সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নিয়োগের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়। কিন্তু এর মধ্যেও একাডেমিক বিবেচনায় সাউন্ড ব্যক্তিদের বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বেছে নিলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিবেশ ও মানোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে হয়। এসব কথা বলার কারণ হলো আজকে আমরা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে কম গুরুত্ব দিচ্ছি। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কোনোভাবেই কল্যাণকর হতে পারে না। মেধাকে লালন করতে না পারলে ভালো ছাত্র বা ভালো গবেষক তৈরি করা সম্ভব হবে না।
র্যাংকিংয়ে পিছিয়ে পড়ার আরেকটি বড় কারণ হলো এখন গবেষণা কম হয়। এর জন্য যে পর্যাপ্ত তহবিল বরাদ্দ প্রয়োজন তা দেয়া হয় না। শুধু বিজ্ঞান নিয়েই যে গবেষণা হবে তা নয়। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলোতেও গবেষণা হওয়া দরকার। গবেষণা নিবন্ধ ও বই প্রকাশে কোনো প্রণোদনা নেই। এটা স্বীকার করতেই হবে যে, মেধাবী শিক্ষার্থীকে যদি শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিতে না পারা যায় তাহলে মেধাবী শিক্ষক কোথা থেকে পাওয়া যাবে? এ কারণে আমাদের ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশটির কিছুটা সংস্কার করা প্রয়োজন।
দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠতে পারলে এবং দলীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে শিক্ষক পদে মেধাবীদের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হবে। সাধারণত যেকোনো বিভাগে মেধা তালিকায় প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অধিকারীদের আশা থাকে তারা শিক্ষক হবে। তাদের মতামত নেয়া হলে বেশির ভাগ দেখা যাবে শিক্ষক হতে চায়। তাদের আশা থাকে শিক্ষক হয়ে পিএইচডি করবে, গবেষণা করবে। শিক্ষক হওয়া আলাদা ধরনের সম্মানের বিষয়। সম্মানী প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষকরা খুব একটি এগিয়ে না থাকলেও আমাদের সমাজে তাদের সম্মান এখনো অনেক বেশি। আমার অনেক ছাত্র আমার চেয়ে অনেক বেশি টাকা বেতন পায়। এতে আমি বরং গর্ব অনুভব করি। যেকোনো অনুষ্ঠানে যখন যাই তখন শিক্ষক হিসেবে যে সম্মান পাই তা অন্য পেশায় গেলে পেতাম কিনা সন্দেহ আছে। এই সম্মান তো পয়সা দিয়ে কে-না যায় না।
মেধার মূল্যায়ন, শিক্ষকদের গবেষণা ও প্রকাশনায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা, কোনো শিক্ষক বিদেশের কোনো সেমিনার-সিম্পোজিয়াম থেকে আমন্ত্রণ পেলে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে সেখানে যাওয়া-আসা ও থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা, এসব কার্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবারো প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে খ্যাতি ফিরে পাবে বলে আমার বিশ্বাস। সরকারের জন্য এসব খাতে তিন-চার শ’ কোটি টাকার তহবিলের ব্যবস্থা করা কঠিন কিছু নয়।
পরিশেষে বলতে চাই অতি গণতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ক্ষতিকর। সেখানে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। নির্বাচনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। সিনিয়র শিক্ষকদের নীতিনির্ধারণী কার্যক্রমের সাথে বেশি সম্পৃক্ত করতে হবে। হ
লেখক : ফেলো, বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্স এবং সাবেক ডিন ও অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
মেইল : cmhasan@gmail.com
[সূত্র : নয়া দিগন্ত]